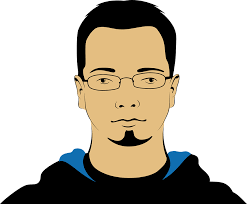

আলেয়া রহমান
দেশ যেদিন স্বাধীন হয়, সেদিন আমার জন্ম ষোলই ডিসেম্বর। তাই প্রতিবেশীরা আমাকে ‘জয়বাংলা’ নামে ডাকতেন। রেললাইন পেরিয়ে বিশাল ধান ক্ষেতের মাঠ। ক্ষেতের শেষ সীমানায় একটি উঁচু টিলায় আমাদের বাড়ি। টিলার পাশ দিয়ে বয়ে গেছে গাগরা ছড়া নামের পাহাড়ি খাল। টিলার আশপাশে ছিল গভীর জঙ্গল। এ জঙ্গলের মধ্যখানে ছোট্ট বাড়িতেই আমার শৈশব-কৈশোর কেটেছে। জঙ্গল জুড়ে ছিলো বুনো ফল আর ফুলের সমাহার। ভাটফুল, লজ্জাবতী, দাদ মর্দন, পিশাস, শিয়াল কাঁটা, লুটকি, আরো নাম না জানা কতো ফুল। ফলের মধ্যে ছিল, টেকাটোকি, পোড়াছয়া, বন বরই, মাটাং, এনুর, রামকলা, বেত, করই জাম, গোলাপ জাম, লুকলুকি, লুটকি। শৈশবে এসব বুনো ফলই ছিলো আমার প্রিয় খাবার। বনে ছিল নানান জাতের পাখ-পাখালি। ভাইয়ের সাথে ‘করল্লা’ নামের ফাঁদ দিয়ে পাখি ধরতে গিয়েছি। ফেরার পথে হাতে এক খাঁচা পাখি নিয়ে বাড়ি ফিরতাম। আমি পড়তাম ভাটেরা হাই স্কুলে। স্কুলে যাবার পথে রেললাইন হতে পাথর কুড়িয়ে নিতাম, বাড়িতে ফিরে খেলতাম ফুলগুটি। পথ থেকে কেনা চার আনার আইসক্রিম চুষে স্কুলের বারান্দায় পা রেখেছি। পাঁচ পয়সার হজমি, দশ পয়সার লেভেন চুষ, খলি মিঠাই আর হাওয়াই মিঠাই ছিল স্কুলে আসা যাওয়ার পথে নিত্যদিনের সঙ্গী।
বাবা ছিলেন কোরআনে হাফেজ। মক্তবে শিক্ষকতা করতেন। আমরা আট ভাইবোন। আমি সবার ছোট। বাবা সন্তানদেরকে পড়াশোনা শেখাতে খুব উৎসাহী ছিলেন। এজন্যে ভাইদের সাথে আমরা বোনদেরকেও স্কুলে ভর্তি করেছিলেন। নইলে আজ নামটাও হয়তো লিখতে পারতাম না। বাবা ছিলেন খুবই শিক্ষানুরাগী মানুষ। আমাদের এলাকায় স্কুল, মসজিদ, মাদ্রাসা, পোস্ট অফিস প্রতিষ্ঠায় তাঁর ছিলো গৌরবজনক অবদান (আল্লাহ বাবাকে জান্নাতবাসী করুন)।
আষাঢ় মাসে বৃষ্টির পানিতে গাগরার জল ফুলে উঠতো, আমরা সেই পানিতে সাঁতার কাটতাম। মাছ ধরতাম। আমার ভাইয়েরা বন থেকে মৌমাছির চাক ভেঙ্গে ডলু বাসের চোঙ্গায় ভরে নিয়ে আসতেন। কত মজা করে খেতাম। ভোর হলে টিলার পাশের বনে ডেকে ওঠতো বন মোরগ। চোখ কচলাতে কচলাতে উঠে দৌঁড় দিতাম শিউলী গাছের তলায়। দু’হাত ভরে যখন ফুল নিয়ে ঘরে আসতাম তখন ঘরের পাশের চিনি বটগাছে তোতা পাখির ডাক শুনতে পেতাম। তোতা পাখির ঝাক যখন বটগাছের টুকটুকে লাল পাকা ফল টুকটুক করে খেত তখন তাদের ঠোঁট এবং গায়ের সবুজ রং আরো সুন্দর লাগতো। আমি ফুল হাতে তাদের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে তাদের সৌন্দর্য উপভোগ করতাম।
বাড়ির পাশের বনে ছিল বন্য শূকর, সজারু, শিয়াল, খরগোশ, গুইসাপ, হরিণসহ আরো কতসব পশু। সন্ধ্যে হলে শিয়াল কাঁটা বনে শিয়ালগুলো হুক্কা হুয়া বলে ডেকে উঠতো। খরগোশরা দল বেধে লাউ ক্ষেতে এসে কচি লাউ কড়মড় করে খেয়ে যেত। তাড়িয়ে দিলে কান খাড়া করে দৌঁড় দিত। বাড়ির পাশের বনে সজারু চুপি চুপি হাঁটতো। মানুষের পায়ের শব্দ পেলে তারা গায়ের কাটা ফুলিয়ে বনের ভিতর দৌঁড় দিত। দেখে মনে হতো বড়ো কোন কদম ফুল ছুটে চলেছে।
চৈত্রের রাত। আকাশ ভরা তারা। বাতাস খাওয়ার জন্য মা উঠানে পাটি বিছিয়ে আমাদের নিয়ে বসতেন। মার ছিলো বই পড়ার অভ্যাস। তিনি আমাদেরকে ‘আনোয়ারা’, ‘আব্দুল্লাহ’, ‘বিষাদসিন্ধু’-র গল্প বলতেন। কান পেতে শুনতাম। আর মাঝে মাঝে আকাশের তারা গুণতাম। মা ছিলেন ব্রিটিশ আমলে পঞ্চম শ্রেণিতে বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রী। সেই সুবাদে তিনি বাংলা, আরবি, নাগরী এসব জানতেন। অনেক ফারসি কবিতা ছিলো মায়ের মুখস্থ। মায়ের কাছে গল্প শুনে শুনে শীতল বাতাস এসে গায়ে লাগত। তখন উঠানেই ঘুমিয়ে পড়তাম।
হেমন্তের মাঠে মাঠে ছিল ফড়িংয়ের খেলা, গাছে গাছে প্রজাপতির মেলা, আঁধার রাতে জোনাকির মিটি মিটি আলো, ছাতিম গাছে হুতুম পেচার ডাক। রাবেয়া, মালতি, বানেছা, জয়নু এদের সাথে গাগরা থেকে মাছ ধরে বনের মাঝখখানে টিলার উপর বনভোজন করতাম। এ বাড়ির ও বাড়ির গাছের তুতফুল, মাটাং ফল, জাম পেড়ে খেতাম। বনে ঘুরে বেড়াতাম। এখন মনে হয় ইস্ এ জীবন যদি আবার ফিরে পেতাম।
আমার অনেক সহপাঠী ও বন্ধু ছিল। কিন্তু সুলতানা জান্নাত শাহানা ছিল আমার একমাত্র কাছের বন্ধু। তৃতীয় শ্রেণি থেকে একইসাথে আমাদের পথচলা। হাত ধরাধরি করে একসাথে হাঁটতাম। ক্লাসে পাশাপাশি বেঞ্চে বসতাম। প্রাইমারির গন্ডি পেরিয়ে আমরা হাইস্কুলে ভর্তি হলাম। এক ক্লাস থেকে অন্য ক্লাসে উঠলাম। বৃষ্টির দিনে কেউ স্কুলে আসুক আর না আসুক আমি আর শাহানা ঝড়, বৃষ্টি উপেক্ষা করে ছাতা মাথায় কাক ভেজা হয়ে স্কুলে আসতাম। আমাদের উপস্থিতি ছিল ষোলআনা। আমি গল্পের বই পড়তে ভালোবাসতাম। কিন্তু, পাঠ্যবইয়ের গল্প, কবিতা ছাড়া সবকিছু ছিল নাগালের বাইরে। লাইব্রেরি কোথায়? গল্প, উপন্যাসের বই কোথায় পাওয়া যায় তা জানতাম না। কারণ বাবা দোয়াত, কলম, বইখাতা এসব কিনে দিতেন। বই পাওয়ার একমাত্র উপায় ছিল বিয়েশাদী। আত্মীয়-স্বজন কারো বিয়ে হলে উপহার হিসেবে বই উঠতো। তখন ভাগ্য খুলতো বই পড়ার। শাহানা একটা বই পেলে আমাকে দিত। আমিও মাঝে মাঝে পেয়ে যেতাম। শাহানা ছিল ফাঁকিবাজ। সে বই না পড়ে আমাকে দিয়ে পড়াতো। পরের দিন যা পড়তাম তার কাছে কাহিনী বলতে হত। এক সময় বইয়ে পড়া সমাজের দুঃখ বেদনা, প্রেম-বিরহের কাহিনী বলতে বলতে চোখ ভিজে বুক ভারী হয়ে যেত। মনে হতো আমিও যদি কিছু লিখতে পারতাম।
কাশেম বিন আবু বকরের ‘ফুটন্ত গোলাপ’ দিয়ে আমার বই পড়ার শুরু। তারপর রোমেনা আফাজের ‘বাসর রাতের স্বপ্ন’, ‘দস্যু বনহর’ ইত্যাদি পড়া। আমার বই পড়ার জায়গা ছিল টংগীঘরের মাটির বারান্দা। সে বারান্দায় বড় হাতলওয়ালা একটি চেয়ার পাতা থাকতো। সামনে ছিল বাড়িতে ওঠার রাস্তা। পাশে বড় একটা শিউলী ফুলের গাছ। বই পড়তে পড়তে আমার লেখক হবার ইচ্ছে হতো। মাঝে মাঝে আমি দু’চার লাইন কবিতা লিখতাম। আবার ছিঁড়ে ফেলতাম। শাহানাকেও দেখাতাম না। কেমন যেন লজ্জা লাগতো।
এক সময় আমার বিয়ে হয়ে যায়। সংসার জীবন, ছেলেমেয়ে এসব নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। দীর্ঘসময় বই পড়া বা কবিতা লিখা আর হয় না। তবে বেতার থেকে সম্প্রচারিত অনুরোধের আসরের গান, সুচন্দা, ববিতা আর শাবানার ছবি দেখতে ভুলতাম না। মাঝে মাঝে কিশোর বাংলা আর বিচিত্রা পড়তাম। এগুলো পাওয়ার সৌভাগ্য হত আমার সহোদর ভাই ডা. আমিনের কাছ থেকে। তিনি তখন সিলেট ওসমানী মেডিকেলে পড়তেন। বাড়ি গেলে এসব নিয়ে যেতেন।
আস্তে আস্তে ছেলে মেয়ে বড় হল। তাদের পড়ার উদ্দেশ্যে সিলেট শহরে চলে আসি। ছেলে মেয়ে তখন অনেক বড়ো হয়ে গেছে, মেয়ে কলেজে পড়ে। আমার খানিকটা অবসর মেলে। আমি লিখতে শুরু করি। কবিতার চেয়ে গদ্য লিখতে আমি স্বচ্ছন্দ বোধ করি। একটা খাতায় আস্তে আস্তে লিখে ফেললাম অনেক গল্প। নিজে লিখি আর নিজেই কাটাকুটি করি। কাউকে দেখাই না। আমিন ভাই তখন ডাক্তার হয়ে ইংল্যান্ডে চলে গেছেন। একদিন ডা. আমিন ভাই ও আর ভাবী ইংল্যান্ড থেকে দেশে আসলেন। তারা জিন্দাবাজারে আল হামরায় একটি ফ্ল্যাট নিলেন। আমিও গেলাম সেখানে। আমিন ভাই ছিলেন আমার বন্ধুর মতো। আমার সব আনন্দ-বেদনার কথা তাকে বলতাম। তিনিও ছিলেন আমার একজন মনোযোগী শ্রোতা। একদিন ভাইকে লেখাগুলো দেখালাম। এই প্রথম কাউকে আমার লেখার খাতা পড়তে দিই। লেখাগুলো পড়ে তিনি যেন চমকে উঠলেন। খুব উৎসাহ দিলেন। ভাই যখন বললেন লেখা ভালো হয়েছে, তখন সত্যি সত্যি আমার মনে হলো লেখা হয়েছে। ভাই বললেন বই বের করে ফেলো। ভাবীকে আমার গল্পের কথা বললেন, ভাবীও খুশি। ভাবী তার ব্যাগ থেকে পঞ্চাশ পাউন্ডের দুটো আমার হাতে ধরিয়ে বললেন, বীণা বই বের করে ফেলো। টাকা আরো লাগলে বলবে। ওহ্ আমার পরিবারের সবাই আমাকে বীণা ডাকেন।
ভাইয়ের উৎসাহ আর ভাবীর টাকা পেয়ে আমারও শখ চাপলো বই বের করবো। কিন্তু বই কিভাবে বের করতে হয়, আমি কিছুই জানিনা। কোন লেখক বা প্রকাশকের সাথেও আমার কোন পরিচয় নেই। কার সাথে যে পরামর্শ করবো ভেবে পাচ্ছিলাম না।
এক দুপুরে আমি কুমারপাড়া থেকে বাসায় ফিরছিলাম। হঠাৎ চোখে পড়লো ‘পা-ুলিপি প্রকাশন’ লেখা একটি সাইনবোর্ড। মনের মধ্যে একটু আশার আলো সঞ্চারিত হলো। রাস্তাটা ঢালু। সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে রিক্সাওয়ালাকে বললাম এই যে রিক্সাটা থামান। রিক্সাওয়ালা কষে ব্রেক ধরে। বলল, কী হইছে আপা? এত তাড়াহুড়ো করছেন কেন? বললাম রিক্সাটা সাইট করে একটু অপেক্ষা করুন। বলে রিক্সা থেকে নামি। মানিক পীরের টিলা, চারপাশে অসংখ্য কবর। আর টিলার গা ঘেসেই পা-ুলিপি প্রকাশনের অফিস। ত্রস্ত পায়ে আমি পান্ডুলিপি অফিসে ঢুকে পড়ি। কম্পিউটারের সামনে বসে আছেন আব্দুল মোমেন সাহেব। নামটা পরে জেনেছি। আমি তাকে সালাম দিয়ে বললাম, এখানে কী বই প্রকাশ করা হয়। আমার সালাম শুনে তিনি ফিরে তাকালেন এবং বললেন, হ্যাঁ। আমার মনে আশার আলো জেগে উঠলো।
বললাম, আমার একটা বই ছাপাতে চাই। বইটি ছেপে দিবেন? তিনি বিনয়ের সাথে বললেন, নিয়ে আসবেন। পরদিনই পা-ুলিপি নিয়ে তাদের অফিসে যাই। পা-ুলিপি জমা দেবার এক সপ্তাহ পর মোমেন সাহেব ফোন দিয়ে বললেন, লেখাটা কম্পোজ করে রেখেছি নিয়ে যাবেন এবং প্রুফ দেখে জমা দিয়ে দিবেন। তাহলেই বইয়ের কাজ শুরু করবো।
মনের আনন্দে দেরি না করেই কম্পোজ করা কপিটা নিয়ে আসি। সেই প্রথম বইয়ের হরফে আমার লেখা। কথা মত প্রুফ দেখে ফেরত দিয়ে আসি। তিনি আমাকে একটা প্রচ্ছদ দেখালেন, এটাই পছন্দ করে দিলাম। পান্ডুলিপি প্রকাশনের স্বত্বাধিকারী বায়েজিদ মাহমুদ ফয়সলকে আমি চিনতাম না, দেখাও হয়নি। বইটি অতি যতœ সহকারে করে দিলেন। তার সাথে পরে দেখা হয়। তাও বই বের হবার পাঁচ-সাত বছর পর। সে অতি ন¤্র আর ভদ্র। আমাকে বড় বোনের মত দেখে। দোয়া করি তার পান্ডুলিপি প্রকাশন যেন আরো প্রসারিত হয়। অনেক দূর এগিয়ে যায়।
একসময় খবর আসে আমার বই হয়ে গেছে। শাহানাকে নিয়ে নতুন বই আনতে যাই। আমার প্রথম বই-‘ভালোবাসার অনেক রকম’। নতুন বইয়ের ঘ্রাণ আমাকে নতুন এক ঘোরে আচ্ছন্ন করলো। বার বার উলটে-পালটে বইটি দেখতে থাকি। আনন্দ-উত্তেজনায় রাতে ঠিক মতো ঘুমও হয় না। জীবনের প্রথম বই ‘ভালোবাসার অনেক রকম’, বইয়ের স্বাদে যেন অতৃপ্ত আত্মা তৃপ্তিতে ভরে যায়। প্রথম বই আমার বোন কবি ও শিক্ষক জুলেহা বুলবুলকে দিলাম। শাহানাকে দিলাম। বেশ কয়েকটা বই আমার বড় বোনের ছেলে শহিদুল ইসলাম নিলো। সে একজন ব্যাংক কর্মকর্তা। সে টাকা দিয়ে বই কিনে। টাকা নিতে আমার কেমন লজ্জা করছিলো, সে জোর করে আমাকে টাকা দেয়। তারপর বইগুলো কোন একটা বইমেলায় দেয়। সব বই বিক্রি হয়ে যায়। সে আমাকে উৎসাহ দেয়। আমি উৎসাহিত হয়ে আরেকটি উপন্যাসে হাত দিই। লেখাটি শেষ করে খাতাটা রেখে দিলাম অনেক দিন।
প্রথম প্রকাশনার প্রথম অনুভূতি
আমার একটি বই বের হয়ে গেলে কি হবে, তখনো সিলেটের সাহিত্য জগতের কাউকে চিনতাম না। সিলেটের সাহিত্য অঙ্গনের প্রিয়মুখ, প্রিয় ছড়াকার শাহ মিজান। সে আমার তালতো ভাই ভাটেরার শ্রদ্ধাভাজন ও প্রিয়মুখ শাহ আজিজ পারুল ভাইয়ের ছেলে। আমাদের বাড়ি থেকে কিছু দূর পথ এগুলেই তাদের বাড়ি। তাই ছোটবেলা থেকেই আমার ভাইয়ের ছেলেদের সাথে খেলাধুলা করে সে বড় হয়েছে। কখনো ভাবতে পারিনি সেই শাহ মিজান আমাকে সিলেটের সাহিত্য জগতে নিয়ে আসবে।
মিজান দেখতে বড়ো হয়ে গেলো। শাহজালাল বিশ^বিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা শেষ করলো। হঠাৎ একদিন তার বিয়ের কার্ড নিয়ে আমার বাসায়। অমা, সেই পিচ্ছি মিজান এখন বিয়ে করতে যাচ্ছে। কার্ড দিয়ে যাবার সময় তার ছড়ার বই ‘নভেম্বরের নয়’ আমার হাতে দেয়। বাহ্ মিজানের ছড়ার বইও বেরিয়ে গেছে। অবাক হয়ে বইটি আমি উলটে পালটে দেখতে থাকি। মিজান জানতো আমিও লেখালেখি করি। বললো নতুন কিছু লিখেছি কি না। আমি খুব আগ্রহে আমার নতুন উপন্যাস ‘নিরধি’র পান্ডুলিপিটা তাকে দেখালাম। পা-ুলিপিটা দেখে শাহ মিজান বললো, ফুফু আব্বা চাচাই’র প্রকাশনা থেকে বইটি বের করে নেন। তার চাচাই লুৎফুর ভাই। আমার তালতো ভাই। মিজানের পরামর্শে আমি পা-ুলিপি নিয়ে লুৎফুর ভাই’র কাছে যাই। লুৎফুর ভাই মনের মাধুরী মিশিয়ে তার হাকালুকি প্রকাশন থেকে বইটি বের করে দেন। তখন সিলেটে কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের বইমেলা ২০১৬ শুরু হচ্ছে। মিজান বললো কেমুসাস’র বইমেলায় ফুফু আপনার বইয়ের প্রকাশনা অনুষ্ঠান করেন। আমি বললাম, বাবা আমি তো কাউকে চিনি না। কিভাবে প্রকাশনা উৎসব করতে হয় আমি জানিনে। তুমি দায়িত্ব নিলে আমি রাজি।
শাহ মিজান আমার নিরধি উপন্যাসের প্রকাশনার আয়োজন করে দেয়। সিলেটের সাহিত্য অঙ্গনের প্রিয় ব্যক্তিত্ব, সকলের প্রিয়মুখ শ্রদ্ধাভাজন গল্পকার সেলিম আউয়ালের মাধ্যমে বইয়ের প্রকাশনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সেলিম আউয়াল ভাই মিজানের ‘নভেম্বরের নয়’ বইয়ে মিজানের পরিচিতি লিখেছেন। তাকে তখনো আমি চিনতাম না। তবে নাম শুনেছি, আমার মেঝভাই ডক্টর নূরুল ইসলামের সাথে তার খুব জানাশোনা। মিজানই সেলিম ভাইয়ের সাথে কথা বলে প্রকাশনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। প্রকাশনার দু’তিন দিন আগে একটি খামে ভরে সাহিত্য সংসদের অফিসে তার জন্যে নিরধি উপন্যাসটি রেখে আসি।
তারপর কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের বইমেলায় আমার বইয়ের প্রকাশনা অনুষ্ঠান হলো। পত্রিকায় নিউজ আসলো—–। সেদিন রাতে আমার ঝুলিতে সকলের হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা ও এক মুঠো স্বপ্ন নিয়ে বাসায় ফিরি।
সেই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সিলেটের লেখকদের সাথে আমার একটি ভালোবাসার সেতুবন্ধন রচিত হয়। সেই থেকে শাহ মিজানের ফুফু, আমি হয়ে গেলাম সিলেটের অসংখ্য তরুণ-তরুণী লেখকের ফুফু। তারা যখন ফুফু ডাকে মন ভরে যায় আনন্দে।
লেখক : উপন্যাসিক ও গল্পকার